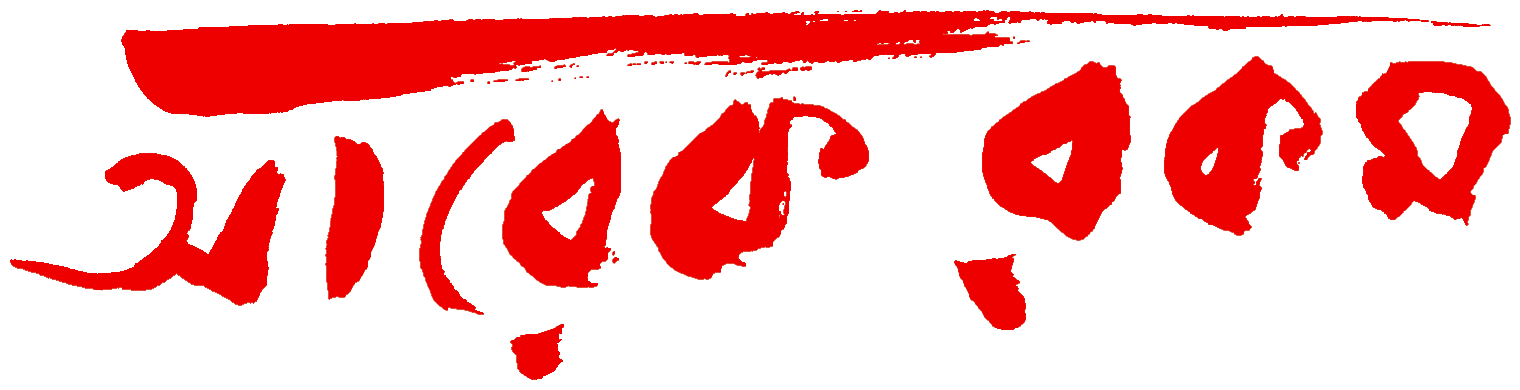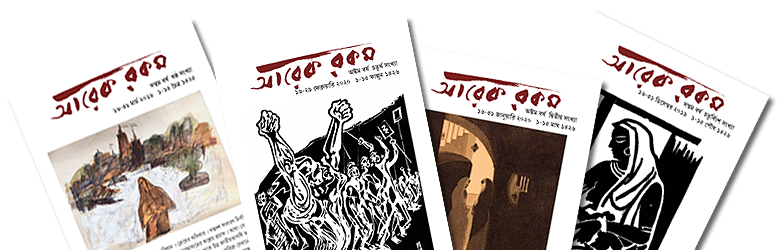আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যা ● ১-১৫ আগস্ট, ২০২৪ ● ১৬-৩১ শ্রাবণ, ১৪৩১
প্রবন্ধ
শিবঠাকুরের আপন দেশে - দ্য কিউরিয়াস কেস অফ নিউজক্লিক (পর্ব ১)
রঞ্জন রায়
সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি. ওয়াই. চন্দ্রচুড় বিগত ১১ই মে, ২০২২ তারিখে রাষ্ট্রদ্রোহ আইন সম্বন্ধিত প্রশ্নে একটি ঐতিহাসিক রায় দিয়ে বলেন ব্রিটিশ জমানার সিডিশন ল’ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা ভারতীয় দণ্ড সংহিতার ধারা ১২৪এ দিয়ে যত কেস দেওয়া হয়েছে তাদের বিচার স্থগিত রাখতে। কারণ, এই আইনটি আজ স্বাধীন ভারতে কতটুকু প্রাসঙ্গিক সেটা বিচার করতে হবে।
প্রধানমন্ত্রী বললেন - বেশ, তাই হবে।
কিন্তু ২২তম ল’ কমিশন তার ২৭৯তম রিপোর্টে ওই ধারা এবং আইন বজায় রাখার সুপারিশ করল। তারপর ভারত সরকার ১১ই আগস্ট, ২০২৩ সালে দেশের ক্রিমিনাল ল' সংশোধনের উদ্দেশ্যে তিনটি বিল আনল যার মাধ্যমে ইন্ডিয়ান পেনাল কোড, ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোড এবং ইন্ডিয়ান এভিডেন্স অ্যাক্ট বাতিল হবে। তারপর ডিসেম্বর মাসে প্রায় বিরোধীশূন্য সংসদে বিনা বিতর্কে সেই বিল তিনটি পাশ হয়ে রাষ্ট্রপতির মোহর লেগে নতুন তিন আইন হয়ে গেল।
বলা হল আগের তিনটে আইন ঔপনিবেশিক প্রভুর পক্ষে এবং ভারতের নাগরিকদের দণ্ড বা শাস্তি দিতে ব্যবহৃত হচ্ছিল। নতুন আইনে ‘দণ্ড’ শব্দ নেই, আছে ‘ন্যায়’। এই আইনগুলো আমাদের ন্যায় দেবে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেবে, সাধারণ নাগরিকদের পক্ষ নেবে।
গত ১ জুলাই, ২০২৪ থেকে ওই তিনটি আইন বলবৎ হয়েছে। সেই আইন মোতাবেক অভিযোগ এবং ধরপাকড় শুরু হয়েছে। কিন্তু আইনগুলো তাদের ঘোষিত লক্ষ্যপূরণে কতদূর সফল হবে? বিধি-বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন?
সেটা বোঝার জন্য আমাদের একটু পিছিয়ে যাওয়া দরকার। এরমধ্যেই ইউপিএলএ (সন্ত্রাস দমন), পিএমএলএ (মানি লন্ডারিং) আইনে - তাদের ২০১৯-র সংশোধিত চেহারায় - এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি) এবং সিবিআই ও পুলিশকে লাগামছাড়া ধরপাকড়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
দেখতে হবে আগের আইনে, ৩০শে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত, কীভাবে নাগরিকের মৌলিক অধিকারের উপর অঙ্কুশ চলেছে। তবেই নতুন আইনের ভালমন্দ এবং আশঙ্কার কারণগুলো বোঝা যাবে।
দ্য কিউরিয়াস কেস অফ 'নিউজক্লিক'
‘নিউজক্লিক’ ওয়েব পোর্টালের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থকে দিল্লির স্পেশাল পুলিশ বিগত ৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে গ্রেফতার করে। তার আগে পোর্টালের দিল্লি-এনসিআর এবং মুম্বাইয়ের অফিসে খানাতল্লাসি চালানো হয়। পুলিশ পরঞ্জয় গুহঠাকুরতা, অভিসার শর্মা এবং আরও ক’জন প্রথিতযশা সাংবাদিককে - যাঁরা কখনও ওই পোর্টালে রিপোর্ট লিখে বা প্যানেল ডিসকাশনে অংশগ্রহণ করেছেন - সারাদিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে।
প্রবীরের বিরুদ্ধে এফআইআর-এ বলা হয় তিনি তাঁর পোর্টালের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিরোধী কাজে লিপ্ত।
যেমন, কাশ্মীর এবং অরুণাচল প্রদেশকে ‘ভারতের অংশ নয়’ বলা, সরকারের কোভিডের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তাচ্ছিল্য করা, কৃষকদের ধর্না-আন্দোলনকে আর্থিক সাহায্য করা আর চিনা টেলিকম কোম্পানির মামলায় ওদের পক্ষ নিয়ে ‘স্পিরিটেড’ লড়াই করা। আরও বলা হয় - 'নিউজক্লিক' চিনের থেকে ঘুরপথে আর্থিক সাহায্য পেয়েছে।
মামলা শুরু হয়। -নিউজক্লিক'-এর মানবসম্পদ বিভাগের প্রধান অমিত চক্রবর্তী জানুয়ারি ২০২৪-এ রাজসাক্ষী হয়ে বলেন যে অভিযোগটি সত্যি - এই পোর্টাল চিনের পক্ষে প্রচার করার জন্যে বিদেশি অর্থসাহায্য পায়। দিল্লি হাইকোর্ট ৮ মে তারিখে অমিতকে জেল থেকে মুক্তির আদেশ দেয়।
অঘটন আজও ঘটে
কিন্তু এরপরে এল ‘কাহানি মেঁ টুইস্ট’। সুপ্রীম কোর্ট গত ১৫ মে তারিখে রায় দিল যে 'নিউজক্লিক'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রবীরবাবুর ইউএপিএ’র অধীনে ‘গ্রেফতার’ এবং তারপরের পুলিশি ‘রিমান্ড’ অবৈধ। অতএব, অভিযুক্তকে তৎকাল জামিনের বণ্ড ভরিয়ে ছেড়ে দেওয়া হোক।
জাস্টিস বি. আর. গগই এবং জাস্টিস সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ কলমের এক খোঁচায় খারিজ করে দিলেন ৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখের গ্রেফতারির আদেশ, ৪ তারিখের রিমান্ড অর্ডার এবং দিল্লি হাইকোর্টের ১৩ অক্টোবর তারিখের আদেশ যা উক্ত গ্রেফতার এবং রিমান্ডকে বৈধ ঠাউরেছিল।
প্রবীরবাবু সুপ্রীম কোর্টের আদেশের কয়েক ঘন্টা পরে জেলের বাইরে বেরিয়ে খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিলেন।
সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ভিত্তি কী?
গোটা ব্যাপারটায় সরকার-পুলিশ-প্রশাসনের আইনের বিধিসম্মত পদ্ধতি বা ‘ডিউ প্রসেস অফ ল’ পালন না করা।
এককথায় বলতে গেলে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার সময় তাঁকে বা তাঁর উকিলকে গ্রেফতারের কারণটি 'লিখিত' ভাবে জানানো হয়নি। না জানালে অভিযুক্ত তার উকিলের সঙ্গে নিজের ডিফেন্সের জন্য কোনো অর্থপূর্ণ পরামর্শের সুযোগ পাবেনা। তাতে সংবিধানের আর্টিকল ২০, ২১ এবং ২২-এর মাধ্যমে 'জীবন এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা'র যে মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে তা লঙ্ঘিত হয়েছে। বেঞ্চের মতে ওই অধিকার হল - “most sacrosanct fundamental right any attempt to violate such fundamental right - would have to be dealt with strictly”.[১]
বাস্তবে কী হয়েছিল?
প্রবীর পুরকায়স্থের বিরুদ্ধে এফআইআর (২২৪/২০২৩) করা হয়েছিল ১৭ই আগস্ট, ২০২৩ তারিখে। কিন্তু এটা দিল্লি পুলিশ তাদের পোর্টালে আপলোড করেনি। ফলে ব্যাপারটা জনসাধারণের গোচরে ছিলনা। প্রবীরবাবুকে ৩ অক্টোবর গ্রেফতারের সময় তাঁকে বা তাঁর উকিলকে কারণ জানানো হয়নি। এমনকি এফআইআর-এর কপিও পরে ৫ তারিখে দেওয়া হয়। কিন্তু পুলিশ কাস্টডিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রিমান্ড অর্ডার তো আগের দিন ৪ তারিখে পাস হয়ে গেছে।
গ্রেফতারের ‘কারণ’ ও গ্রেফতারের ‘ভিত্তি’
সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বেঞ্চ তাঁদের রায়ে গ্রেফতারের ‘কারণ’ ও ‘ভিত্তি’র মধ্যেকার ফারাকটা স্পষ্ট করেছেন।
‘কারণ’ হল যা সব অপরাধী বা অভিযুক্তকে গ্রেফতারের সময় জানানো হয় - আরেকটা অপরাধ না করতে অগ্রিম ব্যবস্থা, প্রমাণ নষ্ট করার সুযোগ না দেওয়া, সাক্ষীকে ভয় দেখানোর সুযোগ না দেওয়া ইত্যাদি।
‘ভিত্তি’ হল যা প্রত্যেক অপরাধী বা অভিযুক্তের গ্রেফতারের জন্য আলাদা। অর্থাৎ সে কোন বিশেষ অপরাধ করেছে সেটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া।
কিন্তু প্রবীরবাবুর কেসে অ্যারেস্ট মেমোতে শুধু গ্রেফতারের ‘কারণ’ বা ‘রীজন’ বলা রয়েছে। ভিত্তি বা গ্রাউন্ডের কোনো উল্লেখ নেই।
দিল্লি পুলিশের এ'বিষয়ে বক্তব্যঃ
এক, পুরকায়স্থকে গ্রেফতারের সময় যে অ্যারেস্ট মেমো দেওয়া হয়েছিল সেটাই ‘গ্রাউন্ড’ বোঝার জন্য যথেষ্ট।
দুই, যেহেতু অভিযুক্তকে রাষ্ট্রদ্রোহের কঠিন সব কেস দেওয়া হয়েছে তাই মহামান্য আদালত যেন গ্রেফতারের ‘গ্রাউন্ড’ বিধিবদ্ধভাবে জানানো হয়েছে কি হয়নি তা নিয়ে অযথা কালাতিপাত না করেন।
সুপ্রীম কোর্ট দুটো যুক্তিই নাকচ করে দিয়ে বলেন - অ্যারেস্ট মেমো হল একটা বাঁধাগতের প্রোফর্মা মাত্র যাতে খালি গ্রেফতারের ‘রীজন’ বলা হয়।
গ্রেফতারের সময়?
দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল প্রবীর পুরকায়স্থকে গত বছর অক্টোবরের ৩ তারিখে ভোর সাড়ে ছ’টায় গ্রেফতার করে। মূল অভিযোগ - পয়সা নিয়ে চিনের হয়ে দেশে প্রচার করা।
তাঁকে ইউএপিএ’র ধারা ১৩ (বে-আইনী কাজকর্ম), ধারা ১৬ (সন্ত্রাসবাদী কাজ), ধারা ১৮ (ষড়যন্ত্র), ধারা ২২সি (কোম্পানী দ্বারা অপরাধ); এবং ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ধারা ১৫৩এ (দুটো সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈমনস্য সৃষ্টি করা), আর ১২০বি (অপরাধ করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র) লাগিয়ে কেস দেওয়া হয়।
তারপর তাঁকে তক্ষুণি একজন স্পেশাল জজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রিমান্ড নেবার জন্য পেশ করা হয়। এরপর বেলা সাতটায় হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তাঁর উকিলকে গ্রেফতারের খবর জানানো হয়, তবে সেখানে সময় এবং গ্রেফতারের ভিত্তি কি সেটার কোনো উল্লেখ ছিল না।
কিন্তু বেলা আটটায় রিমান্ড নিয়ে আপত্তি পেশ করলে জানা যায় তার অর্ডার তো আগেই পাশ হয়ে গেছে! আর সেই অর্ডার সাইন করার সময় দেখাচ্ছে সকাল ৬টা। অর্থাৎ অভিযুক্তকে জজের বাড়িতে হাজির করার আগেই সেটা তৈরি ছিল। তাতে দেখা যাচ্ছে যে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত প্রবীর পুরকায়স্থকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ কাস্টডিতে সাত দিন রাখার অনুমতি দিয়েছেন।
মাননীয় শীর্ষ আদালত লক্ষ্য করেছেন যে জজ পরে দুটো লাইন যোগ করে লিখেছেন যে পুলিশের পুরকায়স্থকে রিমান্ডে চাওয়ার আবেদন অভিযুক্তের উকিলকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি রিমান্ড অর্ডারে ওই দুটো লাইন যে পরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তা সাদা চোখেই দেখা যাচ্ছে।
তাই প্রবীরের আবেদনের সার হল যে গ্রেফতারি এবং রিমান্ড আইনি পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া (ডিউ প্রসেস অফ ল') মেনে হয়নি।
সুপ্রীম কোর্টও কেসের মেরিটে নয়, (মামলা শুরুই হয়নি) পদ্ধতিগত খামতির কারণে সরকার পক্ষের সমস্ত আপত্তি খারিজ করে প্রবীর পুরকায়স্থের জামিন মঞ্জুর করেন।
বর্তমান রাষ্ট্রের দুটো ড্রাকোনিয়ান আইনের (ইউএপিএ এবং পিএমএলএ) গ্রেফতারি এবং বিনা বিচারে আটকের প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এই নাগরিকের অধিকার রক্ষার জন্য এই রায় এবং 'ডকট্রিন অফ ডিউ প্রসেস' যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার আগে ‘রিমাণ্ড’ ব্যাপারটা দেখে নেয়া যাক।
‘রিমান্ড’ শুনানিতে কী হয়?
আমরা প্রবীর পুরকায়স্থের কেসের উদাহরণেই আলোচনা সীমিত রাখব।
গ্রেফতারের পর মুখ্য ভূমিকা ম্যাজিস্ট্রেটের। সংবিধানের আর্টিকল ২২(২) বলছেঃ প্রত্যেক গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির করতে হবে।
এটাকে বলে ‘ফার্স্ট প্রোডাকশন’। শুনানির পর ম্যাজিস্ট্রেট বা সেশন জজের অধিকার উনি অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদে’র জন্য 'পুলিশ কাস্টডি'তে ছেড়ে দেবেন (একদিন বা অধিকতম ১৫ দিন), অথবা পুলিশের জিম্মায় না দিয়ে 'জুডিসিয়াল কাস্টডি' বা জেলে পাঠাবেন।
এটা কোনো যান্ত্রিক বা ঔপচারিক পদ্ধতিগত ব্যাপার নয়। এখানে ম্যাজিস্ট্রেটকে জুডিসিয়াল স্ক্রুটিনির মাধ্যমে খুঁটিয়ে দেখতে হয় যে বিধিসম্মত এবং সংবিধানসম্মত মানবাধিকারের সমস্ত রক্ষাকবচ - শুধু অক্ষর ধরে নয়, আইনের অন্তর্নিহিত ভাবনাকে সম্মান করে - পালন করা হচ্ছে কিনা।
কিন্তু এই বিষয়ে একটি রিসার্চ বলছে পুরকায়স্থ কেসে সুপ্রীম কোর্ট যেসব পদ্ধতিগত ত্রুটির দিকে আঙুল তুলেছেন তা কোনো ব্যতিক্রম নয়। বেশিরভাগ ম্যাজিস্ট্রেটই অভিযুক্তের ‘ফার্স্ট প্রোডাকশন’ যে আইনি এবং সাংবিধানিক সুরক্ষা কবচ দেয় তার গুরুত্ব নিয়ে সম্যক অবহিত বা সচেতন নন।[২]
অধিকাংশই কেবল দেখে নেন যে ফাইলে অ্যারেস্ট মেমো (যাতে গ্রেফতারের স্থান, পরিস্থিতি, সময়, পরিবারের কাউকে খবর দেওয়ার তথ্য) এবং মেডিকো লীগ্যাল সার্টিফিকেট বা এমএলসি (অভিযুক্তের ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট) দেওয়া আছে কিনা।
নিঃসন্দেহে এগুলো কাউকে বে-আইনি গ্রেফতারি এবং পুলিশি অত্যাচারের থেকে বাঁচানোর ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলছে এ’ব্যাপারে কাগজগুলো ঠিকভাবে তৈরি করা হয় না।
• অ্যারেস্ট মেমো অনেক সময় আদালতে দাঁড়িয়ে ভরা হয়, আগে নয়।
• ম্যাজিস্ট্রেট কদাচিৎ কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অভিযুক্তকে প্রশ্ন করে অ্যারেস্ট মেমোয় দেওয়া তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাই করেন। অথচ থানার ভেতরে অভিযুক্তের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা হয়েছে, ডাক্তারি পরীক্ষা ঠিকমতো হয়েছে কিনা এগুলো যাচাই না করলে কীভাবে অভিযুক্তের বিধি এবং সংবিধানসম্মত অধিকার রক্ষা করা সম্ভব?
• অ্যারেস্ট মেমো এবং ডাক্তারি পরীক্ষার সার্টিফিকেটের কোন স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট নেই।
• সুপ্রীম কোর্ট যেভাবে পুরকায়স্থ জামিনের রায়ে গ্রেফতারির 'রীজন' (যা কমন) এবং 'গ্রাউন্ড' (যা কেস স্পেসিফিক) এর মধ্যে তফাত স্পষ্ট করে দেখিয়েছেন তাতে বোঝা যায় যে শুধু অ্যারেস্ট মেমো দেখলে ‘ডিউ প্রসেস অফ ল’ পালন করা হয়েছে কিনা - তা বোঝা সম্ভব নয়।
• অধিকাংশ রিমান্ডের শুনানি অভিযুক্তের উকিলের অনুপস্থিতিতেই হয়ে যায়।
• রিমান্ড উকিলেরা, যাঁরা নামমাত্র ফী নিয়ে বা না নিয়ে প্রি-ট্রায়াল স্টেজে অভিযুক্তের পক্ষে দাঁড়ান, তাঁরা অধিকাংশ সময় শুধু এফআইআর-এর কপি পেয়ে সন্তুষ্ট থাকেন। অ্যারেস্ট মেমো এবং এমএলসি রিপোর্ট চাওয়ার দরকার মনে করেন না। যদিও এগুলি পাওয়া অভিযুক্তের মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে।
• ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশাসনিক কাজের চাপ অনেক বেশি। একটা সাধারণ ধারণা হয়ে গেছে যে প্রি-ট্রায়াল ফার্স্ট প্রোডাকশন নেহাত নিয়মরক্ষার ব্যাপার। তাই এগুলো দায়সারাভাবে করা হয়। আদালতে অভিযুক্তকে পেশ করার সময় কেবল পুলিশের কথার উপর নির্ভর করা হয়।
রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার 'নিউজক্লিক'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থের জামিন দেওয়ার সময় সুপ্রীম কোর্টের বেঞ্চের রায় প্রি-ট্রায়াল স্টেজে ‘ডিউ প্রসেস অফ ল’-এর গুরুত্বকে বিশেষ করে তুলে ধরেছে।
ডিউ প্রসেস অফ ল’ কী?
আর্টিকল ২২(১) বলছেঃ কোন ব্যক্তিকেই আটক করার আগে যত শীঘ্র সম্ভব তার কারণ না জানিয়ে তাকে গ্রেফতার করা যাবে না। এবং তাকে তার পছন্দের উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করার এবং নিজের আত্মরক্ষার জন্য তার সাহায্য নেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।
প্রবীর পুরকায়স্থের গ্রেফতারির দিনই সুপ্রীম কোর্ট একটি মানি-লন্ডারিং কেসে (পঙ্কজ বনসাল বনাম ভারত সরকার) রায় দিয়েছিলেন যে পিএমএলএ (প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট) ধারা ১৯(১) অনুসারে অভিযুক্তকে গ্রেফতারের পূর্বে তাকে আটকের গ্রাউন্ড বা ভিত্তি লিখে জানাতে হবে।
পুরকায়স্থ কেসে জামিন দেবার সময় সরকার পক্ষের আপত্তি ছিল যে পিএমএলএ’র উদাহরণ প্রবীরের কেসে অপ্রাসঙ্গিক। কারণ, প্রবীরকে মানি-লণ্ডারিং নয়, রাষ্ট্রবিরোধী কাজকর্মের জন্য কেস দিয়ে আটক করা হয়েছে।
কিন্তু সুপ্রীম কোর্ট এই আপত্তি নাকচ করে জানিয়েছেন যে ওঁদের মতে ইউএপিএ ধারা ৪৩বি(১) এবং পিএমএলএ ধারা ১৯(১)-এর মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। ভাষা এবং শব্দের হিসেবেও প্রায় এক। আসলে এদের দুটোরই উৎস হল সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারের আর্টিকল ২২(১)।
অতএব, যত কঠোর অপরাধের ধারায় কেস দেওয়া হোক না কেন - তাতে সরকার বা পুলিশের ইচ্ছেমতো যেমন তেমন করে গ্রেফতার করা যাবে না। কাউকে তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে হলে পুলিশ এবং প্রশাসনকে বিধিসম্মত পদ্ধতি মেনে চলতে হবে।
এইভাবেই ‘ডিউ প্রসেস অফ ল' ডকট্রিন’ রাষ্ট্রের এবং প্রশাসনের স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবহারের, বিশেষ করে, রাষ্ট্রের সুরক্ষা তথা দেশদ্রোহের চার্জ লাগিয়ে যখন তখন যেমন খুশি ধরপাকড়ের চেষ্টার বিরুদ্ধে ঢাল হয়েছে।
অথচ এই ডকট্রিন নতুন কিছু নয়। ম্যাগনা কার্টা (১২১৫) হচ্ছে বিশ্বে মানবাধিকারের প্রথম সনদ। তাতেও এই পদ্ধতিগত ‘ফেয়ারনেস’ বা ন্যায়পরায়ণতার নীতির কথা বলা হয়েছে।
“no freeman shall be seized or imprisoned or stripped of his rights - except by the lawful judgement of his co-equals or by the law of the..."[৩]
হায়দ্রাবাদের 'ন্যাশনাল আকাডেমি অফ লীগ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ' (নালসার)-এর প্রাক্তন উপ-কুলপতি এবং সংবিধান-বিশেষজ্ঞ ফৈজান মুস্তাফা বলছেন যে, আসলে Fifth Amendment to the American Constitution (1791) পাকাপোক্তভাবে 'due process' ধারণাটিকে আইনের আওতায় নিয়ে এল।
উনি এও বলছেন যে আইনের 'due process' মাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকার নয়। এটি একটি সভ্যতার পরিপক্কতার কালোত্তীর্ণ মাপদণ্ডও বটে।
ভারত ওই মাপদণ্ডে কোথায় দাঁড়িয়ে?
উপসংহার
আমরা জানতাম - ভারতের ক্রিমিনাল জুরিসপ্রুডেন্স বা অপরাধ আইনের নীতি অনুসারে ‘অপরাধ আদালতে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সবাই নির্দোষ’ এবং ‘জেল নয় জামিন’টাই সাধারণ নিয়ম। কিন্তু যখন থেকে কিছু ‘স্পেশাল’ আইন শুরু হয়েছে - মানি লণ্ডারিং আটকাতে পিএমএলএ, মাদকদ্রব্যের সেবন ও তস্করী ঠেকাতে এনডিপিএসএ, সন্ত্রাসবাদকে নিয়ন্ত্রণ করতে ইউএপিএ - ততই গ্রেফতারের বিরুদ্ধে জামিন পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে।
এমনকি কাউকে সন্দেহের বশে ধরে এনে বিনা চার্জ, বিনা বিচারে মাসের পর মাস, বছরের পর আটকে রাখা আমাদের চোখে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।
শারীরিকভাবে অক্ষম হুইলচেয়ারে বসে থাকা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হানিবাবু, জে.এন.ইউ.-এর ছাত্রনেতা উমর খালিদ, অশীতিপর কবি ও মানবাধিকার দুই কর্মী ফাদার স্ট্যান স্বামী এবং ভারভারা রাও, সাংবাদিক গৌতম নওলাখা এর কিছু উদাহরণ। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের যে স্ট্যান স্বামী জেলেই বিনা বিচারে মারা গেলেন।
সেই পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে আর্টিকল ২২(১) এবং ডিউ প্রসেস অফ ল’-এর গুরুত্ব রেখাঙ্কিত করা নিঃসন্দেহে আশা জাগায়।
কিন্তু হায়দ্রাবাদের 'ন্যাশনাল আকাডেমি অফ লীগ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ (নালসার)-এর প্রাক্তন উপ-কুলপতি এবং সংবিধান-বিশেষজ্ঞ ফৈজান মুস্তাফা মন্তব্য করেছেনঃ প্রবীর পুরকায়স্থের রিমান্ড কেসের শুনানিতে ভারপ্রাপ্ত অ্যাডিশনাল সেশন জজ খুব দায়সারাভাবে বিগত ৪ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে ভোর ৬টায় অভিযুক্তের জন্য সাতদিনের পুলিশ কাস্টডির রায় দিলেন।
উনি দেখলেন না যে অভিযুক্তের উকিলকে খবর দেওয়া হয়নি এবং গ্রেফতারের আধার বা গ্রাউন্ড জানানো হয়নি। ফলে অভিযুক্ত নিজের পক্ষে বা পুলিশের হাতে সঁপে দেওয়ার বিরুদ্ধে কোন ডিফেন্স করতে পারেনি।
অথচ, দুই গবেষক জেবা সিকোরা এবং জিনি লোকনীতা বলছেন সুপ্রীম কোর্টের রায়ে ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব এবং সতর্কতা নিয়ে কিছু বলা হয়নি!
কাজেই এখনও দিল্লি দূর-অস্ত্! আমাদের পথচলা শুরু হয়েছে মাত্র।
(চলবে)
তথ্যসূত্রঃ
১) ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৬ মে, ২০২৪।
২) জেবা সিকোরা ও জিনি লোকনীতা, ‘Magistrates & Constitutional Protections: An Ethnographic Study of First Productions and Remands in Delhi Courts’।
৩) ফৈজান মুস্তাফা, 'এ রাইট টু ফেয়ারনেস', ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ১৭ মে, ২০২৪।