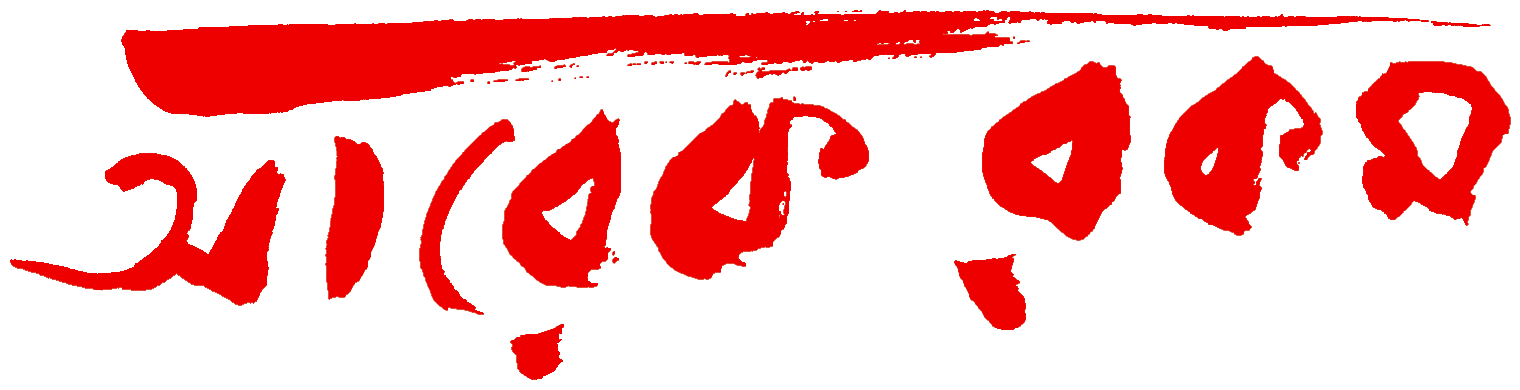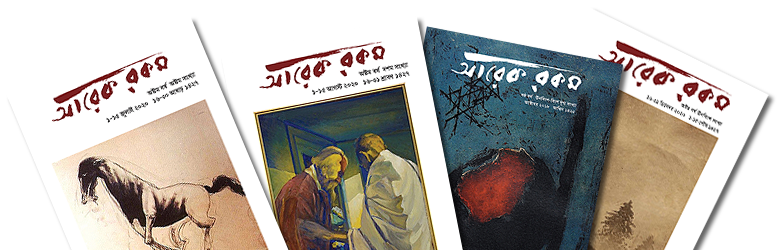আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যা ● ১-১৫ আগস্ট, ২০২৪ ● ১৬-৩১ শ্রাবণ, ১৪৩১
প্রবন্ধ
গ্যাভিন মুনীঃ এক পথিকৃৎ অর্থশাস্ত্রী
অমিয় কুমার বাগচী
আমি প্রথমে বলি আমার সঙ্গে কীভাবে গ্যাভিন মুনী (Gavin Mooney) এবং ডেল (ডেলিস) ওয়েস্টন (Del Weston)-এর আলাপ এবং বন্ধুত্ব হয়েছিল। আমি ২০০৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহরে কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'হেডন উইলিয়ামস ফেলো' হিসাবে গিয়েছিলাম। গ্যাভিন তখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য অর্থনীতির অধ্যাপক। তিনি আমার বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন। তারপর থেকেই আমাদের আলাপ এবং অল্পদিনের মধ্যেই গভীর বন্ধুত্ব হয়। তিনি তাঁর নববিবাহিত পত্নী ডেল ওয়েস্টনকে নিয়ে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। 'Institute of Development Studies Kolkata'-তে তখন প্রয়াত অধ্যাপক পঞ্চানন চক্রবর্তীর নামে একটি স্কলারশিপ ছিল। গ্যাভিন দুই বৎসর সেই স্কলারশিপের টাকা দিয়েছিলেন। ডেল ছিলেন কমিউনিস্ট। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে অনেক কাজ করেছিলেন এবং তার জন্য তাঁকে কারাবরণ করতে হয়েছিল। গ্যাভিন এবং ডেল, গ্যাভিনের অবসরগ্রহণের পর টাসমেনিয়ায় একটি বাড়ি করেছিলেন। ডেলের আগের পক্ষের বিয়ের দুটি পুত্রসন্তান ছিল। বড় ছেলে নিক অপ্রকৃতিস্থ ছিল। সে টাসমেনিয়ায় গিয়ে গ্যাভিন এবং ডেল দুজনকেই ১৯ ডিসেম্বর, ২০১২ সালে হত্যা করেছিল। গ্যাভিনের বয়স তখন ৬৯ বৎসর আর ডেলের বয়স ৬২ বৎসর। ডেল মৃত্যুর আগে 'The Political Economy of Global Waring' নামে একটি খুব উঁচুদরের বই লিখেছিলেন, সেটি ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটির কথায় পরে আসব।

গ্যাভিন গ্ল্যাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক হন। তারপর কিছুদিন ইনসিউরেন্স কোম্পানিতে এবং তারপর ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিসে কাজ করেন। তখনই তাঁর মনে হয়েছিল যে সে দেশের সরকারি স্বাস্থ্যনীতিতে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না। তিনি ১৯৭৭ সালে অ্যাবর্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Aberdeen, Scotland) গিয়ে 'Health Economics Research Unit' (HERU) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংস্থায় চিকিৎসাশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রের যোগ নিয়ে গবেষণা শুরু হয়। গ্যাভিন এটি ১৯৭৭ থেকে ১৯৮৬ এবং ১৯৯১ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত পরিচালনা করেন।
স্বাস্থ্যপরিষেবা সম্বন্ধে গ্যাভিনের প্রশ্ন ছিল যে, কে রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়? রোগী নিজে, বা ডাক্তার, না হাসপাতাল, না সরকার? নব্য উদারনীতির পরিবেশে এখন সিদ্ধান্ত নেয় হাসপাতাল, এবং ডাক্তার হাসপাতালের নিয়োজিত লোক বলে ডাক্তারকে হাসপাতালের কথা ভাবতে হয়। হাসপাতাল একটি লাভমুখী সংস্থা। সুতরাং ডাক্তারকে ভাবতে হয় কীভাবে হাসপাতালের লাভ বাড়ানো যায় - রোগীর স্বার্থ সেখানে গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। অথচ রোগীর স্বার্থই সেখানে প্রধান বিষয় হওয়া উচিত। স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত অর্থশাস্ত্রেও এই বিষয় প্রায়ই উপেক্ষিত থাকে।
সাধারণ জ্ঞান থেকেই বলা যায় যে সামাজিক কিছু ব্যাপার স্বাস্থ্যের নির্ণায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু ২০০৮ সালে WHO-র 'Commision on Social Determinants of Health' প্রকাশিত হবার পর স্বাস্থ্য পরিষেবা পরিমণ্ডলে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। গ্যাভিনের মতে আর্থিক দিক থেকে উন্নত দেশগুলির মধ্যে এ বিষয়ে যত আলোচনা হয়েছে, গরিব দেশগুলির স্বাস্থ্যপরিষেবার উপরে সেভাবে আলোকপাত করা হয়নি। গরিব দেশগুলির সমস্যা হল অধিকাংশ লোকের পানযোগ্য জলের অভাব, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, বাসযোগ্য বাড়ির অভাব, শিক্ষার অভাব, ডাক্তারের অভাব, স্বাস্থ্যপরিষেবা আহরণ করার ক্ষমতার অভাব ইত্যাদি। পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ লোক থাকে গরিব দেশগুলিতে। এবং সেই দেশগুলিতে একটি বড় গোষ্ঠী হল আদিবাসী গোষ্ঠী। আদিবাসীরা সাধারণত থাকেন প্রত্যন্ত প্রদেশে - যেখান থেকে প্রধান নগর, ক্ষমতার পীঠস্থানগুলি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলি দূরে থাকে এবং আদিবাসীরা সেই প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেতে পারেন না। তাছাড়া সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত পার্থক্যের জন্যও আদিবাসীরা এই প্রতিষ্ঠানগুলির পরিষেবা গ্রহণ করতে ভয় পান।
এ বিষয়ে বলিভিয়ার একটি সিনেমা 'Blood of the Condor' খুবই উল্লেখযোগ্য। বলিভিয়ার পাহাড়ি অঞ্চলে আমেরিকান 'Peace Corps'-এর একটি দল ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। তাদের উদ্দেশ্য হল সেই অঞ্চলের আদিবাসীদের স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়া, কিন্তু আসল উদ্দেশ্য তাদের নির্বীর্য্যকরণ। সে কথায় পরে আসছি। Peace Corps-এর একজন লোক দেখলেন একজন মহিলা তরিতরকারি, মুরগী ইত্যাদির পসার নিয়ে বসে আছেন। তিনি তা কিনতে চাইলে মহিলা বললেন তিনি তাকে কিছু বিক্রি করতে পারবেন না, কারণ চার মাইল দূর থেকে তাঁর খরিদ্দাররা আসবে, তারা সেগুলো পাবে না। আদিবাসীরা যখন জানতে পারল যে Peace Corps-এর আসল উদ্দেশ্য কী তখন তারা হাসপাতালটা গুঁড়িয়ে দিল। এই আক্রমণের ফলে দুই পক্ষের কিছু লোক মারা গেল এবং বলিডিয়ার সরকার আদিবাসীদের অনেককে গ্রেপ্তার করল। কিন্তু Peace Corps-কে সেখান থেকে পাততাড়ি গোটাতে হল।
এবার গ্যাভিনের কথায় ফিরে আসি। গ্যাভিন দেখলেন যে গরিব মানুষরা অনেক বেশি অসুস্থতাপ্রবণ। তার তিনটি কারণ। প্রথমত, তাদের কাছে পরিশ্রুত পানীয় জল, উপযুক্ত পরিবেশ অলভ্য। দ্বিতীয়ত, নব্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের নিজেদের চিকিৎসার জন্যে যে টাকা দরকার তা তারা পায় না। তৃতীয়ত, তাদের কাছে ডাক্তার, হাসপাতাল অতীব শক্তিশালী বোধ হয় এবং তারা তাদের কাছে যেতে ভয় পায়।
'World Health Organisation' (WHO) পৃথিবীর সমস্ত মানুষের স্বাস্থ্যপরিষেবার জন্য গঠিত হয়েছে। কিন্তু মুশকিল হল যে WHO-র বিশেষজ্ঞরা প্রায়শই পশ্চিমের ধনী দেশগুলির অবস্থা দিয়ে সমস্ত দেশের লোকের বিচার করে। তাদের আয়ের বৈষম্য, তাদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য চোখে পড়ে না। ফলে সেই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ প্রায়শই কোনো গরিব লোকের (এমনকি ধনী দেশগুলির গরিবদেরও) কাজে লাগে না।
WHO অর্থনীতিবিদ জেফ্রি স্যাকসের সভাপতিত্বে একটি 'Commission on Macroeconomics and Health' গঠন করে এবং সেই কমিশন ২০০১ সালে রিপোর্ট জমা দেয়। কিন্তু মুশকিল হল যে প্রথমত জেফ্রি স্যাকস প্রবলভাবে নব্য উদারনীতির প্রবক্তা। তাঁকে 'পূর্ব ইয়োরোপের কশাই' বলা হত, কারণ তাঁরই সুপারিশে সোভিয়েট পরবর্তী রাশিয়া, রোমানিয়া, মলডোভা, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি নব্য উদারনীতি গ্রহণ করে প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। Macroeconomics and Health কমিশনের রিপোর্টেও তাঁর মনোভাব প্রকটভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল। সমস্ত সুপারিশই ছিল পশ্চিম ইয়োরোপের দানের উপরে নির্ভরশীল - HIV/AIDS, ম্যালেরিয়া, যক্ষা - সব ক্ষেত্রেই পশ্চিম ইয়োরোপের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দানে নিরাময় হবে। মুশকিল হল যে কমিশন যতখানি দানের সুপারিশ করেছিল তা লভ্য হবে না। মধ্যে থেকে গরিব দেশগুলি বড়লোক দেশগুলির খুদকণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে।
গ্যাভিন এরপর এসেছেন 'World Trade Organisation'-এর (বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার) প্রসঙ্গে, বিশেষ করে তার Trade Related Intellectual Property Rights (বাণিজ্য সম্পর্কিত মেধা সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে।
আগের যে 'General Agreement on Trade and Tariff' তার মধ্যে TRIPS-এর কথা ছিল না। Pfizer কোম্পানির শীর্ষাধিকারিক Edward Preete-র ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফলে নতুন WTO চুক্তির মধ্যে TRIPS ঢুকে যায়। আগে আমাদের দেশে মেধাসম্পর্কিত সম্পত্তির মেয়াদ ছিল ১৪ বৎসর, ওষুধের ক্ষেত্রে ছিল ৭ বৎসর। WTO চুক্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুসারে এই মেয়াদ বাড়িয়ে কুড়ি বৎসর করে দেওয়া হয়। এর ফল উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর মারাত্মক হয়। বিশেষ করে স্বাস্থ্যপরিষেবার ক্ষেত্রে। পৃথিবীর বেশিরভাগ ওষুধের মেধাস্বত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং পশ্চিম ইয়োরোপের ওষুধ কোম্পানিগুলির কুক্ষিগত। তাদের উদ্দেশ্য লাভ বাড়ানো, মানুষের মঙ্গল নয়। এই ওষুধগুলির দৌরাত্ম্য মারাত্মক হল যা HIV/AIDS-এর ক্ষেত্রে দেখা দিল। এই রোগ সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত হয়েছিল আফ্রিকা মহাদেশে।
দক্ষিণ আফ্রিকাতে যখন HIV/AIDS-এর প্রাদুর্ভাব হল, তখন কর্পোরেট ঔষধ কোম্পানিগুলির এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক এবং WTO-র ভূমিকা সাংঘাতিক রূপ নিল। একদিকে দক্ষিণ আফ্রিকার খনিজ পদার্থের কোম্পানিগুলি HIV/AIDS-এর প্রসার ঠেকানোর জন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করল না। অন্যদিকে ২০০২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার আন্দোলন করল যাতে যে দামে বিদেশে ওষুধ কোম্পানিগুলি AIDS-এর ওষুধ বিক্রি করছিল তার থেকে সস্তায় যদি পাওয়া যায়। প্রথমে WTO ওষুধগুলির দাম কমাতে রাজি হল। কিন্তু একমাস পরে WTO অন্য পন্থা নিতে বাধ্য হল কারণ এরকম সস্তায় AIDS-এর ওষুধ বেচলে তাদের লাভ কমে যাবে। ১৯৯০-এর দশকে আমেরিকান কোম্পানি AIDS-এর ওষুধ AZT বিক্রি করছিল এবং তার দাম ছিল বছরে ৮,৪৪০ ডলার। সেখানে ভারতীয় কোম্পানি Cipla সেই একই ওষুধ বিক্রি করছিল তার দাম ছিল রোগী পিছু ২ ডলার অর্থাৎ বছরে ৭৩০ ডলার, আমেরিকার ওষুধের দামের এক দশমাংশেরও কম। শেষ পর্যন্ত Cipla-র কম দামের চাপে এবং আমেরিকার একটি AIDS চিকিৎসার ব্যাপারে সক্রিয় একটি সংগঠন যার মুখ্য সংগঠক ছিলেন William Haddad, বহুজাতিক কোম্পানিগুলি আফ্রিকায় তাদের ওষুধের দাম কমাতে বাধ্য হল। তবে দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং আফ্রিকা মহাদেশে এখনও AIDS-এর প্রভাব আছে। তার প্রধান কারণ দারিদ্র্য এবং অসাম্য। আর্থিক অসাম্য মাপা হয় 'Gini' সূচক দিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সেই সূচক ০.৬৭ যা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ।
২০২২ সালে আফ্রিকা মহাদেশে ৩,৮০,০০০ লোক AIDS-এ মারা গিয়েছে। সারা পৃথিবীর একই বৎসরে ৬,৩০,০০০ লোক HIV/AIDS-এ মারা গিয়েছে। অর্থাৎ যেখানে আফ্রিকা মহাদেশে পৃথিবীর লোকসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ লোক বাস করে, সেখানে HIV/AIDS-এ পৃথিবীর বেশি লোক মারা যায় এই মহাদেশে। এখনও দক্ষিণ আফ্রিকার শতকরা ২৫ ভাগ মৃত্যু হয় HIV/AIDS থেকে এবং ২৫ থেকে ৪৯ বৎসরের লোকেদের মৃত্যুর শতকরা ৪০ ভাগ মৃত্যুর জন্য দায়ী HIV/AIDS।
খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য পরিষেবার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ - এটি একদিকে প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ এবং অন্যদিকে খুবই অকেজো। ২০১০ সালে সেদেশের প্রেসিডেন্ট ওবামা স্বাস্থ্য পরিষেবার সংশোধন করার জন্য আইন (The Affordable Care Act - ACA) পাশ করেন। তার ফলে ৩ কোটির বেশি আমেরিকান 'Medicaid'-এর (একটি সরকারি স্বাস্থ্য ইনসিউরেন্স সংস্থা) আওতায় আসবে এবং সরকারি অনুদানের সাহায্যে গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা আরেকটু কম দামে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে পারবে (রিপাব্লিকানরা এই সংস্কারের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিল)। 'Amrican Medical Association' (AMA) উঠেপড়ে 'ওবামা কেয়ার' (PPACA)-র বিরোধিতা করল। তাদের মতে 'ওবামা কেয়ার' স্বাস্থ্যপরিষেবার ব্যাপারে সরকারি হস্তক্ষেপ। অর্থশাস্ত্রে বলে যে স্বাস্থ্যপরিষেবা, শিক্ষাব্যবস্থার মতোই সাধারণ্যের মঙ্গল পরিষেবা - সুতরাং ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও সামর্থ্যের ওপর তা ফেলে রাখা যায় না। AMA-র ডাক্তাররা নিজেদের রোজগার এবং হাসপাতালগুলির লাভের দিকে চোখ রেখেই এই অবস্থান নিয়েছিলেন - গরিব রোগীরা স্বাস্থ্যপরিষেবা থেকে কি পেল না পেল, তা ওঁদের দেখার কথা নয়। আরও আগ বাড়িয়ে অনেকে বললেন যে 'ওবামা কেয়ার' নাকি সমাজতন্ত্রের দিকে এটি বিপজ্জনক পদক্ষেপ। 'ওবামা কেয়ার'-এর সীমিত সংস্কার সত্ত্বেও ধনী দেশগুলির মধ্যে আমেরিকার নাগরিকদের গড় আয়ু সবচেয়ে কম এবং সেই গড় আয়ু কমে যাচ্ছে। আমেরিকার গড় আয়ু হ্রাসের হার এক শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ২০১৪ সাল পর্যন্ত আস্তে আস্তে আমেরিকানদের গড় আয়ু বাড়ছিল। সে বছর তাদের গড় আয়ু ছিল ৭৮.৯ বৎসর। কিন্তু ২০২১ সালে তাদের গড় আয়ু ছিল ৭৬.১ বৎসর - সাত বৎসরে গড় আয়ু ২.৮ বৎসর কমে গিয়েছে।
এবার আসি ব্রিটেনের 'National Health Service' (NHS)-এর কথায়। এই জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্ম হয়েছিল ১৯৪৮ সালে যখন ক্লিমেন্ট অ্যাটলীর নেতৃত্বে লেবার পার্টি সরকারে ক্ষমতাসীন ছিল। NHS-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে সমস্ত নাগরিক বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পাবেন, হাসপাতালগুলি সরকার পরিচালনা করবেন এবং স্বাস্থ্যপরিষেবার খরচ আসবে সরকারি কোষাগার থেকে।
১৯৭৯ সালে মার্গারেট থ্যাচারের নেতৃত্বে টোরীরা ক্ষমতায় আসার পরে NHS-এর ওপর বাজার অর্থনীতির আঘাত বারবার পড়েছে। কিন্তু এই তথাকথিত সংশোধনকারীদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও NHS সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়নি। তার একটা কারণ NHS-কে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত পুঁজির হাতে তুলে না দিলে প্রতিযোগিতা করানো যায় না। NHS অর্ধমৃত অবস্থায় বেঁচে থাকার পিছনে ডাক্তারদের প্রতিরোধও খানিকটা কাজ করেছে। এখন অনেক জায়গায় Private Practice আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানি যে সেগুলি মোটেই পদের নয়।
অন্যদিকে ডেনমার্কে স্বাস্থ্যপরিষেবা সংস্কারের সময় কর্তাব্যক্তিরা গ্যাভিনকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডেকে নিয়েছিলেন। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য ছিল এটা যাচাই করা যে সেদেশের স্বাস্থ্যপরিষেবা কতটা জবরদস্ত ছিল। ১৯৯০-এর দশকে ডেনমার্কের সব অধিবাসীদের - সে নাগরিক হোক বা অধিবাসীই হোক - একটি 'Social Security Card' দেওয়া হতো। তাতে সেই লোকটির Social Security নম্বর, তার ঠিকানা এবং ডাক্তারের ঠিকানা দেওয়া থাকত। সেই লোকটি যাই রোজগার করুক, Social Security নম্বর ধরে সেই রোজগারের খবর সরকারি দপ্তরে পৌঁছে যেত এবং তার ওপর শতকরা ৬০ ভাগ ট্যাক্স দিতে হতো।
গ্যাভিন তাঁর মতবাদ প্রচারের জন্য ২০টির বেশি বই লিখেছিলেন, রেডিয়োতে বলতেন এবং ব্রিটেন ছাড়াও কাজ করেছেন সুইডেন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায়। তিনি দেখেছিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার কীরকমভাবে কট্টর উদারপন্থী হয়ে গিয়েছে, যার একটি ফল হল যে আগেই যা বলেছি, Apartheid-এর পর দক্ষিণ আফ্রিকায় আর্থিক অসাম্য অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং তার প্রভাব সমস্ত Social determinants of health-এর উপর এবং শিক্ষার উপর খুব খারাপ হয়েছে।
কীভাবে কর্পোরেটরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দখল নিচ্ছে তা বোঝাবার জন্য গ্যাভিন পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার একটি ছোট শহর ইয়ারলুপ যার লোকসংখ্যা মাত্র ৬০০ এবং আমেরিকান কোম্পানি 'অ্যালকোয়া' (Alcoa)-র উদাহরণ দিয়েছেন।
১৯৮৪ সালে অ্যালকোয়া ইয়ারলুপ থেকে মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে Wagerup-এ একটি অ্যালুমিনা পরিশোধনের কারখানা স্থাপন করল, ৪,০০০ লোক নিয়োগ করে। ১৯৯০-এর দশকের একটি রির্পোটে বলা হয়েছে যে ইয়ারলুপের লোকেরা এবং অ্যালকোয়ার কর্মীরা প্রায়শই নাক দিয়ে রক্তপড়া, মাথাধরা এবং বিবমিষায় ভুগতে থাকল। ২০০৬ সালে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সরকার Alcoa-র ফ্যাক্টরির বড় রকমের সম্প্রাসারণ মঞ্জুর করল। তার কারণ এতে কর্মসংস্থান এবং আয় বাড়বে। ২০০৬ সালের Alcoa ফ্যাক্টরির সম্প্রসারণের আগে 'Wagerup Medical Protections Association'-এর সভ্যরা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সরকারের 'Environmental Protection Authority'-র কাছে সুপারিশ করেছিল, যে অ্যালকোয়া পরিশোধনাগরের দূষণের ফলে ইয়ারলুপের অধিবাসীদের এবং অ্যালকোয়ার শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের যে ক্রমাগত ক্ষতি হয়ে চলেছে তার প্রেক্ষিতে যেন অ্যালকোয়ার সংশোধনাগারের সম্প্রসারণ না করা হয়। কিন্তু সেই সুপারিশে কোনও লাভ হয়নি। এই সমস্ত জানার পর গ্যাভিন এই ব্যাপারে মাথা দিতে শুরু করলেন। গ্যাভিন আবিষ্কার করলেন যে অ্যালকোয়া তাঁর নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্টিনে একটি 'সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র' (Community Development Centre)-এর টাকা দেয়। 'West Australian' পত্রিকার মুখ্য সাংবাদিক পল মারে অ্যালকোয়ার কারখানা কীভাবে ইয়ারলুপের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেছিল, তা নিয়ে লিখেছিলেন। মারে তারপর গ্যাভিনকে ইন্টারভিউ করতে চাইলেন। গ্যাভিন বললেন যে একটি জনসমাজের লোক যদি একটি স্বাধীনভাবে কোনো সংস্কারে পর্যালোচনা করতে চায়, তবে তারা কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেই যদি কোম্পানির ভূত ঢুকে থাকে, যেমন কার্টিনে অ্যালকোয়ার অনুদানে চলে জনসমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র, তাহলে তারা সেই সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। গ্যাভিন এই ইন্টারভিউ দেওয়ার ফলে কার্টিনের কর্তাব্যক্তিরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু গ্যাভিনের তাতে কিছু যায় আসে নি।
গ্যাভিনের এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি হল দুটি সিদ্ধান্ত প্রথমত স্বাস্থ্যপরিষেবা দেওয়া হবে সহভোগতন্ত্র (Communitarianism)-র মধ্য দিয়ে। প্রত্যেক জনসমাজের নিজস্ব স্বাস্থ্যপরিষেবা থাকবে। প্রয়োজন হলে আরও ওপর স্তর থেকে বিশেষজ্ঞ আনা হবে সরকারের কাছ থেকে টাকা বরাদ্দ হবে, কিন্তু হাসপাতালগুলি থাকবে জনসমাজের নিয়ন্ত্রণে, এবং ডাক্তাররা ব্যক্তিগত পরিষেবা দেবেন না, সবই হবে জনসমাজ-পরিচালিত পরিষেবা। রোগীদের সংস্কৃতি মেনে এই পরিষেবা দেওয়া হবে। গ্যাভিন অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে অনেক কাজ করেছিলেন। আদিবাসীদের সংস্কৃতি এবং জ্ঞানকে মান্যতা দেওয়া হবে। ওড়িশার পর্বত থেকে সেই অঞ্চলের আদিবাসীরা ভেষজ সংগ্রহ করে। তার মানে এই নয় যে আদিবাসীদের নতুন প্রযুক্তির প্রয়োজন নেই। কিন্তু সেই প্রযুক্তি তাঁদের রুচিকে সম্মান করে দেওয়া হবে। গ্যাভিন কিউবার এবং কেরালার স্বাস্থ্য-পরিবেশ সহভোগতন্ত্র-ভিত্তিক পরিষেবার উদাহরণ বলে মনে করেছিলেন।
দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গ্যাভিনের সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্ভাবন। প্রত্যেক জনসমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি নাগরিক জুরি থাকবে। সেই জুরি স্বাস্থ্যপরিষেবা ঠিকমতো চলছে কিনা তা নির্দিষ্ট সময় সময়ে বিচার করবে। প্রত্যেক রোগীকে শুধু উপভোক্তা হিসাবে দেখা হবে না, তাকে নাগরিক হিসাবে সম্মান করা হবে। নাগরিক জুরি দরকার হলে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং সাধারণ পরিবেশ, সুস্থ জীবনযাত্রার পক্ষে যা অনুকূল সে সব বিশেষজ্ঞদের দিয়ে যাচাই করাবেন।