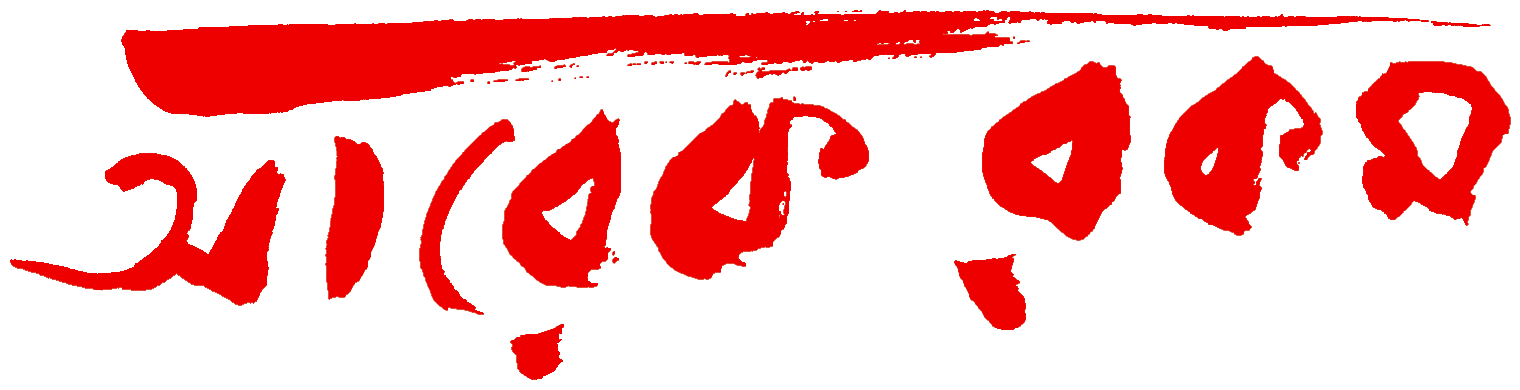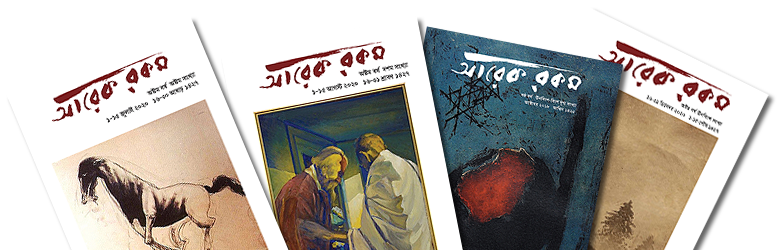আরেক রকম ● দ্বাদশ বর্ষ পঞ্চদশ সংখ্যা ● ১-১৫ আগস্ট, ২০২৪ ● ১৬-৩১ শ্রাবণ, ১৪৩১
সম্পাদকীয়
কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৪-২৫
পিছিয়ে যাওয়া যাক কয়েক মাস। মনে করুন ফেব্রুয়ারি বা মার্চ ২০২৪-এ আপনি রয়েছেন, উলটে দেখুন পুরোনো সংবাদপত্র। বিজেপি নেতাদের রণহুঙ্কার নিশ্চয়ই এখনও শুনতে পাচ্ছেন, যে ‘আবকি বার ৪০০ পার’। ২০২৪ সালের নির্বাচনী লড়াই শুরু হওয়ার আগেই স্বঘোষিতভাবে নিজেদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে দিয়েছিল বিজেপি তথা তাদের পোষ্য মিডিয়াকুল। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল বেরোলে দেখা গেল বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে, এনডিএ মেরেকেটে ৩০০টি আসনে জয়ী। এই ফলাফলের বিশদ ব্যাখ্যা আমরা আগেই করেছি। আপাতত এই প্রশ্ন তোলা জরুরি যে নির্বাচনী ফলাফলের পরে পেশ করা প্রথম কেন্দ্রীয় বাজেটে কি মোদী সরকার এমন কোনো বার্তা দিল যে তারা নির্বাচন থেকে কোনো শিক্ষা নিয়েছে?
কোভিড পরবর্তী সময় থেকে এখন অবধি ভারতীয় অর্থব্যবস্থা নিয়ে আলোচনায় তিনটি কথা বারংবার উঠে এসেছে। প্রথমত, দেশে আর্থিক বৈষম্য অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ছাপিয়ে চলে গেছে। দ্বিতীয়ত, দেশে প্রবলভাবে কর্মসংস্থানের সংকট রয়েছে। তৃতীয়ত, দেশে অর্থনৈতিক চাহিদার অভাব রয়েছে, কারণ মানুষের কাছে পর্যাপ্ত আয় নেই যা ব্যবহার করে তারা বাজারে চাহিদা বাড়াতে পারবে। বিজেপি তথা মোদী সরকার এই সমস্ত সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে প্রতিনিয়ত দেশের মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করেছে যে কোনো সমস্যাই নেই। বরং দেশে 'অমৃতকাল' শুরু হয়েছে।
২০২৪-২৫ সালের বাজেটে মূলত আগের বাজেটগুলোর মতই সরকার যে নীতি গ্রহণ করেছে, তার থেকে স্পষ্ট, একমাত্র বেকারত্ব ব্যতিরেকে সরকার আর কোনো সমস্যাকেই গুরুত্ব দিচ্ছে না। যেমন এই বছর বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট খরচ জিডিপি-র অনুপাতে ১৪.৮ শতাংশ, যা বিগত চার বছর ধরে লাগাতার কমছে। কোভিডের সময় এই খরচের অনুপাত বেড়ে হয়েছিল ১৭ শতাংশের বেশি। কিন্তু তারপর থেকে খরচের পরিমাণ লাগাতার কমছে। যদি আমরা বিশ্বাস করি যে দেশের মানুষের আয়ের সমস্যা রয়েছে বা চাহিদার সমস্যা রয়েছে তাহলে জিডিপি-র অনুপাতে সরকারী খরচ বাড়ানো উচিত। কিন্তু সরকার এর ঠিক উলটো পথে হেঁটে খরচ কমাচ্ছে। অর্থাৎ সরকার মনে করছে যে দেশে আসলে চাহিদার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অর্থব্যবস্থায় বিনিয়োগ তথা ভোগ্যপণ্যের উপর খরচের তথ্য বলছে যে চাহিদার সমস্যা রয়েছে। এমনকি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা সহ বহু অর্থনীতিবিদ মনে করছেন যে ভারতে জিডিপি-র বৃদ্ধির হার নিয়ে যেই তথ্য দেওয়া হচ্ছে তা ভ্রান্ত। আসলে জিডিপি বৃদ্ধির হার সরকারী হিসেবের তুলনায় বেশ কিছুটা কম। কিন্তু সমস্ত মতকে বাতিল করে সরকার ব্যয় সঙ্কোচনের নীতি গ্রহণ করে চলেছে।
এই ব্যয় সঙ্কোচন করার প্রধান কারণ আর্থিক ঘাটতিকে কমানো। সরকারী বাজেট ঘাটতি আসলে সরকারের আয় এবং ব্যয়ের ব্যবধানকে বোঝায়। সরকারী আয়ের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল কর। সরকারের মোট কর এবং জিডিপির অনুপাত ২০২৪-২৫ সালে ১১.৮ শতাংশ হবে বলে সরকার অনুমান করছে। ২০২৩-২৪ সালে এই অনুপাত ছিল ১১.৭ শতাংশ এবং ২০২১-২২ সালে ছিল ১১.৫ শতাংশ। অতএব সরকারের রাজস্ব আয় বাড়ছে খুবই ধীর গতিতে। এই প্রবণতার নেপথ্যে রয়েছে অন্য একটি কাহিনি। মোদী জমানায় মোট রাজস্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করের অনুপাত কমেছে। বর্তমানে ৫৭.৭ শতাংশ কর আসে প্রত্যক্ষ কর থেকে যা ২০১৫-১৬ সালের এই অনুপাতের তুলনায় কম। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোদী সরকারের রেকর্ড ভালো নয়। এর প্রধান কারণ হল কর্পোরেট ক্ষেত্রকে ব্যাপক কর ছাড় দেওয়া। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গেছে যে ২০১৪ সালে যেখানে কর্পোরেট কর জিডিপির অনুপাতে ৩.৪ শতাংশ ছিল, তা বর্তমানে কমে হয়েছে ৩.১ শতাংশ। অথচ ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর একই সময়ে জিডিপি-র অনুপাতে ২.১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩.৬ শতাংশ হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে প্রথমবার ব্যক্তিগত আয়কর কর্পোরেট করের থেকে বেশি হয়েছে। যেখানে মোদী সরকার প্রায় রোজ দেশের মধ্যবিত্তের জন্য গলা ফাটায়, তাদের বন্ধু সাজার চেষ্টা করে, সেখানে দেখা যাচ্ছে যে আসলে মধ্যবিত্তের উপর বাড়তি করের বোঝা চাপিয়ে মোদী সরকার কর্পোরেটদের কর ছাড় দিচ্ছে।
সরকারের রাজস্ব আদায়ের এই নীতি দেশে আয় বৈষম্য আরও বৃদ্ধি করবে, কারণ প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ কমছে এবং তার মধ্যেও কর্পোরেটদের কর ছাড় দেওয়ার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ মোদী সরকার কর্পোরেট বান্ধব নীতিসমূহ গ্রহণ করে চলেছে এবং দেশে যে আর্থিক বৈষম্যের সমস্যা রয়েছে তাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করছে। তবু, তথ্য বলছে যে জিডিপি-র অনুপাতে মোট কর সংগ্রহ বেড়েছে। তা সত্ত্বেও জিডিপি-র নিরিখে সরকারী খরচ বাড়ানো হচ্ছে না কারণ বাজেট ঘাটতিকে সরকার কমাতে চাইছে। যখন দেশে চাহিদা এবং আয়ের সমস্যা রয়েছে সেই সময় বাজেট ঘাটতি কমানোর নীতি যে ভ্রান্ত সেই কথা আজ থেকে ৮০ বছর আগে প্রমাণিত হয়ে গেছে। কিন্তু মোদী সরকার সেই ভ্রান্ত নীতি অবলম্বন করেই চলেছে। কারণ বাজেট ঘাটতিকে কম করে রাখলে দেশী এবং বিদেশী পুঁজিপতিদের খুশি রাখা যায়। অর্থনীতিতে এমন তত্ত্বেরও প্রচলন আছে যে বাজেট ঘাটতি কমলে পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ করে। মুশকিল হল যে এইসব ভ্রান্ত তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল হয়ে সরকার এমন নীতি গ্রহণ করছে যা দেশের মানুষের ক্ষতি করছে।
যেখানে বৈষম্য অথবা অর্থব্যবস্থায় চাহিদার সমস্যাকে সরকার কোনোরকম গুরুত্ব দিতে অস্বীকার করেছে, সেখানে বেকারত্ব এবং কর্মসংস্থানের সমস্যা নিয়ে অর্থমন্ত্রী বেশ কিছু নীতিগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নির্বাচনের আগে যেখানে বিজেপি বেকারত্বের সমস্যাকে ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, দাবি করেছিল যে দেশে নাকি কোটি কোটি চাকরি তৈরি হয়েছে, সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা চলে যাওয়ার পরেই বাজেটে তারা স্বীকার করে নিল যে আদতে দেশে বেকারত্বের ভয়াবহ সমস্যা রয়েছে। যদিও সেই সমস্যার সমাধান হিসেবে বাজেটে যেই নীতিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে তা ভ্রান্ত এবং এর ফলে বেকারত্বের মৌলিক সমস্যার কোনো সমাধান হবে না।
বেকারত্ব নিরশনের জন্য সরকার মূলত যেই নীতিসমূহ গ্রহণ করেছে তার মোদ্দা কথা হল এই যে কোনো কোম্পানি যদি কাউকে কর্মসংস্থান দেয় তাহলে তাকে নানান সুবিধা দেওয়া হবে। বিশেষ করে প্রথম চাকরির প্রথম মাসের বেতন সরকার দেবে, দ্বিতীয়ত ম্যানুফাকচারিং ক্ষেত্রে প্রদেয় মজুরির উপরে সরকার ভরতুকি দেবে ইত্যাদি। অর্থাৎ মূলত যেই সংস্থাগুলি চাকরি দেবে তাদের প্রদেয় মজুরির একটি অংশ সরকার দেবে যাতে মজুরির খাতে কোম্পানিগুলির খরচ কমে। যেহেতু তাদের মজুরি কম দিতে হবে তাই কোম্পানিগুলি বেশি করে কর্মসংস্থান তৈরি করবে, এই ধারণার উপর ভিত্তি করেই এই নীতিসমূহ নেওয়া হয়েছে। মুশকিল হল যে এই অর্থনৈতিক তত্ত্ব যা মনে করে যে মজুরি কমালে চাকরি বাড়বে তা ভ্রান্ত। যেকোনো অর্থব্যবস্থায় কর্মসংস্থান নির্ভর করে দেশের মোট চাহিদার উপর। চাহিদা বাড়ানোর জন্য আবশ্যিক বিনিয়োগ বাড়ানো। বর্তমানে ভারতে বেসরকারী ক্ষেত্র বিনিয়োগে খুব বেশি উৎসাহী নয়। এই পরিস্থিতিতে সরকারী বিনিয়োগ বাড়িয়ে অর্থব্যবস্থায় চাহিদা বাড়ানো যেতে পারে। কিন্তু সরকার উলটো পথে হেঁটে সরকারী খরচ কমাচ্ছে আর অন্যদিকে কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য কর্পোরেটদের মজুরির খরচ কমানোর চেষ্টা করছে। এই দুটি নীতি আসলে পরস্পর বিরোধী। যেমন এই বাজেটে সরকার ১০০ দিনের কাজের যোজনায় কোনো বাজেট বরাদ্দ বাড়ায়নি। শহরাঞ্চলে ১০০ দিনের কাজের মতন প্রকল্প শুরু করার কোনো বাসনা মোদী সরকারের নেই। অতএব কর্মসংস্থান বাড়ানো নিয়ে এই বাজেটে অনেক কথা থাকলেও তা বেকারত্বের সমস্যার কোনো মৌলিক সমাধান করতে পারবে না।
বিজেপি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পরে প্রথম বাজেটেই তাদের জোটসঙ্গী চন্দ্রবাবু নাইডুর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং নীতিশ কুমারের বিহারের জন্য কিছু আর্থিক বরাদ্দ এই বাজেটে দিয়েছে। সেই বরাদ্দও ঠিক সরকারী কোষাগার থেকে আসবে কি না, তাও স্পষ্ট নয়। বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে বিদেশী সংস্থার থেকে টাকা পাওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার এই দুই রাজ্যকে সাহায্য করবে ইত্যাদি।
ভারতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিষয়। শুধুমাত্র তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক সুবিধার্থে, জোটসঙ্গীদের সমর্থন পাওয়ার জন্য কোনো বিশেষ রাজ্যকে কিছু টাকা পাইয়ে দেওয়া দেশের কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের সাংবিধানিক পরম্পরার বিরুদ্ধে যায়। কোন ভিত্তিতে বিহার বা অন্ধ্রপ্রদেশকে টাকা দেওয়া হচ্ছে? বাকি রাজ্যরা টাকা পাবে না কেন? এইসব প্রশ্ন ওঠা জরুরি।
আসলে কেন্দ্রীয় সরকার যত টাকা রাজস্ব বাবদ মানুষের থেকে সংগ্রহ করে তার ৪১ শতাংশ রাজ্য সরকারগুলিকে তারা দেয় পঞ্চদশ ফিনান্স কমিশনের সুপারিশ মেনে। এই বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য দাবি জানানো উচিত, বিশেষ করে এই কারণে যে সরকারী উন্নয়নমূলক খরচের সিংহভাগই আসলে রাজ্য সরকারগুলি করে। বিহার এবং অন্ধ্রপ্রদেশকে বাড়তি সুবিধা প্রদান করা মোদীর রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। এই রাজনীতির বিরোধিতা করতে হলে সমস্ত রাজ্যের গণতান্ত্রিক দাবি নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি। আশা করি দেশের বিরোধী শক্তিরা সেই গঠনমূলক আন্দোলনে সামিল হয়ে রাজ্যদের প্রাপ্য টাকার পরিমাণ বাড়াতে উদ্যমী হবেন।